- লিঙ্ক পান
- X
- ইমেল
- অন্যান্য অ্যাপ
জনপ্রিয় পোস্টসমূহ
এর দ্বারা পোস্ট করা
Unknown
মুখস্ত বিদ্যার অর্থই হল, জোর করে গেলানো---- লিখেছেন--Nipa Das ________________________________________________ দশম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে প্রমথ চৌধুরীর " বই পড়া " নামক একটা প্রবন্ধ রয়েছে ! প্রবন্ধ টিতে মুখস্থ বিদ্যার কুফল তুলে ধরা হয়েছিল , সেখানে বলা হয়েছিল , পাস করা আর শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয় , পাঠ্যবই মুখস্থ করে পাস করে শিক্ষিত হওয়া যায় না , পাঠ্যবইয়ের বাইরেও অনেক কিছু শেখার আছে ! আমি সবসময় এই প্রবন্ধটা পড়তাম ! এই প্রবন্ধটি আমার প্রিয় ছিল কারণ এতে আমার মনের কথাগুলো উল্লেখ করা ছিল ! মুখস্থ বিদ্যা সম্পর্কে আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই -- মুখস্থ বিদ্যা মানে শিক্ষার্থীদের বিদ্যা গেলানো হয় , তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর না পারুক ! এর ফলে শিক্ষার্থীরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শক্তি হীন হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে ! উদাহরণ :: আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন যারা শিশু সন্তানকে ক্রমান্বয়ে গরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার ও বলবৃদ্ধির উপায় মনে করেন ! কিন্তু দুধের উপকারিতা যে ভোক্তার হজম করবার শক্তির ওপর নির্ভর করে তা মা জননীরা বুঝতে নারাজ ! তাদের বিশ্বাস দুধ পেটে গেলেই উপকার হবে ! তা হজম হোক আর না হোক ! আর যদি শিশু দুধ গিলতে আপত্তি করে তাহলে ঐ শিশু বেয়াদব , সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ! আমাদের স্কুল - কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাও ঠিক এরকম , শিক্ষার্থীরা মুখস্থ বিদ্যা হজম করতে পারুক আর না পারুক , কিন্তু শিক্ষক তা গেলাবেই ! তবে মাতা এবং শিক্ষক দুজনের উদ্দেশ্যেই কিন্তু সাধু , সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ! সবাই ছেলেমেয়েদের পাঠ্যবইয়ের শিক্ষা দিতে ব্যস্ত , পাঠ্যবইয়ের বাইরেও যে শেখার অনেক কিছু আছে তা জেনেও , শিক্ষার্থীদের তা অর্জনে উৎসাহিত করে না , কারণ পাঠ্যবইয়ের বাইরের শিক্ষা অর্থ অর্জনে সাহায্য করে না , তাই পাঠ্যবইয়ের বাইরের শিক্ষার গুরুত্ব নেই ! শুধু পাঠ্যবই পড়ে কেবল একের পর এক ক্লাস পাস করে যাওয়াই শিক্ষা না ! আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাশ হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে ! পাশ করা আর শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয় , এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই ! বিঃদ্রঃ মাছরাঙা টেলিভিশনের সাংবাদিকের জিপিএ ফাইভ নিয়ে প্রতিবেদনের সাথে আমার পোস্টের কোনো সম্পর্ক নেই ! http://maguratimes.com/wp-content/uploads/2016/02/12743837_831291133666492_4253143191499283089_n-600x330.jpg
- লিঙ্ক পান
- X
- ইমেল
- অন্যান্য অ্যাপ
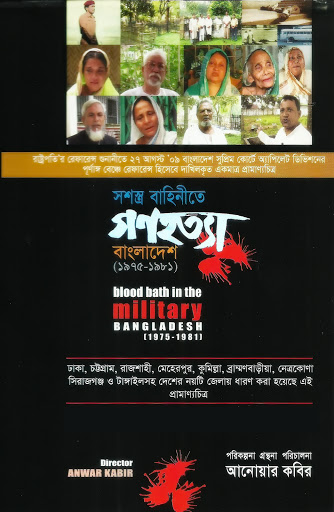

মন্তব্যসমূহ
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন